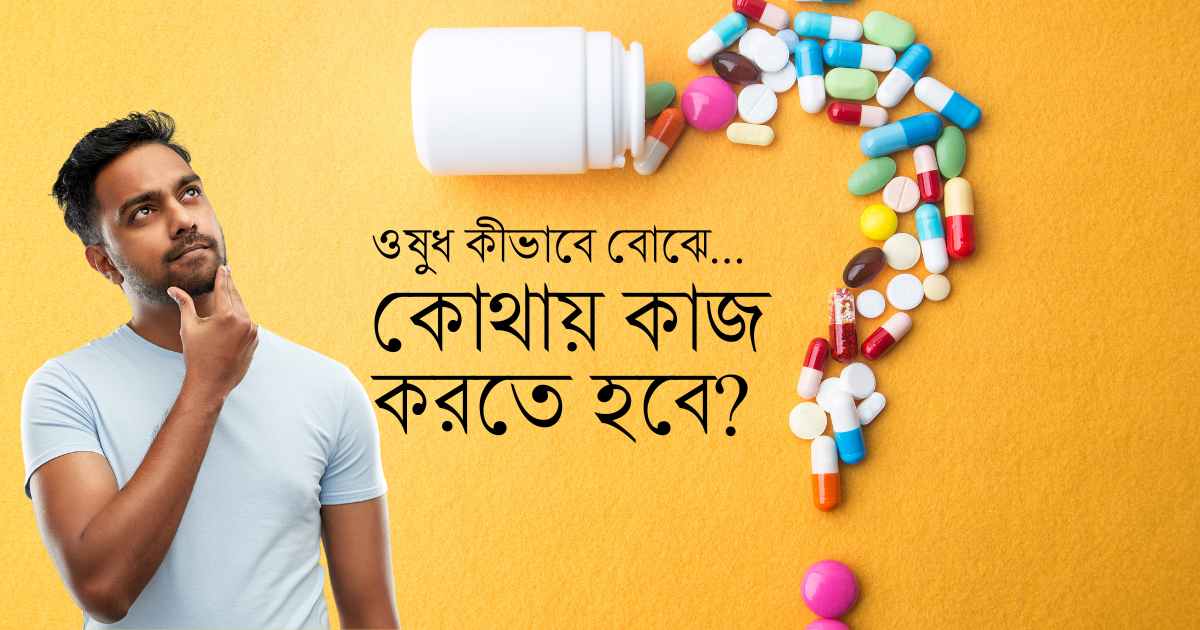আচ্ছা, যখন আমরা কোনো ওষুধ খাই, তখন ওষুধ কীভাবে বোঝে কোথায় কাজ করতে হবে, শরীরের কোন অংশে কাজ করতে হবে? মাথাব্যথা কমাতে হবে, পায়ের ব্যথা নিরাময় করতে হবে, সারা শরীরের অ্যালার্জি দূর করতে হবে বা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে—এটি ওষুধ কীভাবে বুঝে?
কারণ কী? ওষুধের কি কোনো ব্রেন আছে? ওষুধের ভেতরে এমন কী আছে যে, সেটি বুঝতে পারে আমাদের শরীরের ঠিক কোন স্থানে গিয়ে কাজ করতে হবে এবং কীভাবে কাজ করতে হবে?
ছোট্ট একটা জিনিস, এই প্রশ্নটা অনেকের মনেই রয়েছে—তো, চলুন আজকের আলোচনায় আমরা জানার চেষ্টা করি, ওষুধ কীভাবে কাজ করে, এবং শরীরের নির্দিষ্ট সমস্যার সমাধানে কীভাবে ভূমিকা রাখে।
আমাদের দেহে বিভিন্ন ধরনের কার্যপ্রক্রিয়ার জন্য রয়েছে প্রোটিন, তার মধ্যে অন্যতম হলো রিসেপ্টর। রিসেপ্টরগুলো এমন বিশেষ প্রোটিন যা শরীরের কোষের উপর থাকে এবং সেগুলোতে বসেই কোনো ওষুধ তার কাজ করে। প্রতিটি রিসেপ্টর একটি নির্দিষ্ট কাজের জন্য দায়ী, এবং বিভিন্ন কাজের জন্য শরীরে বিভিন্ন ধরনের রিসেপ্টর থাকে।
ছোট্ট একটা উদাহরণ দেই—লোরাটাডিন হলো একটি অ্যান্টি-হিস্টামিন, যা অ্যালার্জি কমানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। এই ওষুধ এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে, বা এর মলিকিউল এমনভাবে তৈরি, যে, ওষুধটি খাওয়ার পর শরীরে গিয়ে সঠিকভাবে হিস্টামিন রিসেপ্টর-এর সঙ্গে যুক্ত হবে।
লোরাটাডিন শরীরে প্রবেশ করার পর, এটি হিস্টামিন রিসেপ্টরকে খুঁজে বের করে এবং সেখানে গিয়ে বাইন্ড করে বসে। এরপর, সেই রিসেপ্টরকে বন্ধ করে দেয়, যাতে শরীরের অতিরিক্ত হিস্টামিন সেখানে গিয়ে বসতে না পারে। এর ফলে, হিস্টামিনের কারণে সৃষ্ট অ্যালার্জির লক্ষণগুলো—যেমন চুলকানি, হাঁচি বা চোখের লাল হওয়া—প্রতিরোধ হয়।
এখন প্রশ্ন আসে, এই বিষয়টা ওষুধ কীভাবে বুঝে? একটা ওষুধের মধ্যে কিন্তু অসংখ্য মলিকিউল থাকে, বিশেষ করে মাইক্রো মলিকিউল। যখন আমরা ওষুধ খাই, এই মাইক্রো মলিকিউলগুলো আমাদের শরীরে প্রবেশ করে এবং রক্তের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।
রক্তে প্রবেশ করার পর, এই মলিকিউলগুলো আমাদের সারা শরীরে ছড়িয়ে যায়। তবে, ওষুধটি কিন্তু শরীরের প্রতিটি জায়গায় গিয়ে বসবে না। এটি শুধু সেই নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে বসবে, যেখানকার জন্য ওষুধটি তৈরি করা হয়েছে।
এটা আসলে কী? এটাকে বলা হয় “Lock and Key” তত্ত্ব, অর্থাৎ তালা-চাবির খেলা। তালা যেমন চাবির সাথে মিললেই খোলে, ঠিক তেমনি ওষুধের মলিকিউলও নির্দিষ্ট রিসেপ্টরের সাথে মিললেই সেখানে গিয়ে কাজ শুরু করে।
ধরুন, আপনার ঘরে দশটি আলাদা আলাদা তালা আছে। এই দশটি তালাকে আপনি একই চাবি দিয়ে খুলতে পারবেন না। প্রতিটি তালায় একটি নির্দিষ্ট চাবিই লাগবে। ঠিক যেমন, প্রতিটি তালায় যে কোন চাবি ফিট করে না, তেমনিভাবে প্রতিটি রোগের জন্য যে কোন ওষুধ কাজ করে না।
ওষুধ তৈরির সময় বিজ্ঞানীরা এই নীতিটিকেই মনে রাখেন। তারা ওষুধকে এমনভাবে তৈরি করেন যাতে সে শরীরের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে ঠিক একটি নির্দিষ্ট কাজ করতে পারে। লোরাটাডিন নামক ওষুধটিও এই নীতি অনুসারেই কাজ করে। এটি শরীরের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে লেগে থাকে এবং অ্যালার্জিজনিত সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে।
আরও জানুনঃ মানুষের জন্য সবচেয়ে বিপদজনক ১০ টি প্রাণী
যখন আমাদের হাত বা পা চুলকায়, তখন আমাদের শরীরে একটি রাসায়নিক পদার্থ তৈরি হয় যাকে হিস্টামিন বলে। এই হিস্টামিন আমাদের শরীরের কিছু নির্দিষ্ট জায়গায়, যাকে আমরা হিস্টামিন রিসেপ্টর বলি, গিয়ে লেগে থাকে।
যখন আমরা এই ওষুধ খাই, তখন ওষুধটি আমাদের শরীরে গিয়ে সেই হিস্টামিন রিসেপ্টরগুলোতে লেগে যায়। এভাবে লোরাটাডিন নামক ওষুধটি হিস্টামিনকে রিসেপ্টরে লেগে থাকতে বাধা দেয় এবং চুলকানি কমিয়ে দেয়।
আরেকটা উদাহরণ দিই—আপনারা হয়তো সালবিউটামল বা লিভোসালবিউটামল নাম শুনেছেন, যা সাধারণত কাশির জন্য বা অ্যাজমার জন্য ব্যবহৃত হয়। আবার, প্রোপ্রানোলল নামটিও হয়তো শুনেছেন।
এই দুটি ওষুধের ধরন আলাদা হলেও, তারা একই ধরনের রিসেপ্টরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করে। তবে, তাদের কার্যপ্রণালী ভিন্ন। যেমন, সালবিউটামল রিসেপ্টরের কাজকে সচল করে দেয়, অন্যদিকে প্রোপ্রানোলল রিসেপ্টরের কাজকে বন্ধ করে দেয়।
একটি উদাহরণ দিলে আরও পরিষ্কার হবে—বিটা ব্লকার যেমন প্রোপ্রানোলল, এটি আমাদের হার্টের Beta 1 receptor এবং ফুসফুসের Beta 2 receptor-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করে।
যখন আমরা প্রোপ্রানোলল খাই, তখন এই ওষুধটি শরীরে প্রবেশ করে এবং একটি নির্দিষ্ট জায়গা খুঁজতে থাকে যেখানে সেটি বসতে পারবে। এই ওষুধের কাজ করার জন্য শরীরে একটি নির্দিষ্ট জায়গা থাকে, যাকে আমরা ‘Key’ বলতে পারি। ওষুধটি এই ‘Key’ খুঁজে পায় এবং হৃদপিণ্ডের দিকে চলে যায়, কারণ হৃদপিণ্ডেই এই ‘Key’-এর জন্য নির্দিষ্ট জায়গা বা ‘Lock’ রয়েছে। হৃদপিণ্ডের পেশীতে গিয়ে, প্রোপ্রানোলল সেই ‘Lock’-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে তার কাজ শুরু করে।
কিন্তু এখানেই শেষ নয়। প্রোপ্রানোলল আবার দেখে, তার জন্য আরেকটি বসার জায়গা আছে—সেটা হলো ফুসফুসের পেশী। ফুসফুসের Beta 2 receptor-এও এই ওষুধ গিয়ে বসতে পারে।
অর্থাৎ, প্রোপ্রানোলল একই সঙ্গে দুটি জায়গায় বসে কাজ করে—হৃদপিণ্ডে এবং ফুসফুসে। কারন সে জানে যে এই জায়গাগুলিতে তার কাজ করার জন্য তালা-চাবির মতো ব্যবস্থা রয়েছে।
অন্যদিকে, যখন আমরা সালবিউটামল বা লিভোসালবিউটামল খাই, সেটি কিন্তু হৃদপিণ্ডে গিয়ে কাজ করে না। কারন হৃদপিণ্ডে যে রিসেপ্টর রয়েছে, সেটি হলো Beta 1 receptor, আর ফুসফুসে আছে Beta 2 receptor। সালবিউটামল ঠিক ফুসফুসের Beta 2 receptor-এ গিয়ে বসবে, কারণ ওষুধের জন্য সেখানেই স্পেসিফিক জায়গা তৈরি করা হয়েছে।
অর্থাৎ বিজ্ঞানীরা এই রিসেপ্টর ও মলিকিউলগুলোর বিশ্লেষণ করে দেখছেন, কীভাবে তারা কাজ করে এবং কীভাবে তাদের কার্যকারিতা প্রভাবিত করা যায়। আর এই বিশ্লেষণের ভিত্তিতে তারা এমন ওষুধ আবিষ্কার করেন, যা রিসেপ্টরগুলোকে বন্ধ বা খুলে দিয়ে দেহের কার্যক্রমকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে।
যেমন ধরুন, আমি যদি খুব সাধারণ ও পরিচিত ওষুধের কথা বলি—ইসোমিপ্রাজল, ওমিপ্রাজল—এই ধরনের ওষুধগুলো কীভাবে কাজ করে? এই ওষুধগুলো মূলত আমাদের পাকস্থলীতে অ্যাসিড তৈরির প্রক্রিয়াকে বন্ধ করে দেয়। কিন্তু কীভাবে এটি করে?
বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন, আমাদের পাকস্থলীতে কিছু বিশেষ কোষ আছে, যেগুলোকে প্যারাইটাল কোষ বলা হয়। এই কোষগুলো পাকস্থলীতে অ্যাসিড তৈরি করে। কিন্তু অ্যাসিড তৈরি করার পেছনে একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া কাজ করে, যার মূল নিয়ামক হলো একটি প্রোটন পাম্প। এই প্রোটন পাম্পের মাধ্যমে পাকস্থলীতে অ্যাসিডের নিঃসরণ ঘটে।
বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন, যদি তারা এমন কোনো ওষুধ তৈরি করতে পারেন, যা প্রোটন পাম্পের কার্যকলাপকে বন্ধ করে দিতে পারে, তাহলে পাকস্থলীতে অ্যাসিড তৈরি হওয়া বন্ধ হবে। তারা আরও বুঝেছেন যে, ওষুধটি এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন এটি আমাদের শরীরের অন্য কোনো অংশে না গিয়ে সরাসরি পাকস্থলীর প্রোটন পাম্পের ওপর কাজ করে। এতে করে, ওষুধটি শুধুমাত্র পাকস্থলীতে অ্যাসিড তৈরির প্রক্রিয়াকে নির্দিষ্টভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে।
তার মানে, ওষুধগুলো এমনভাবে তৈরি করা হয়নি যে আমরা কোনো “ব্রেন” বসিয়ে দিলাম, কিংবা সরাসরি কোনো পরিবর্তন ঘটিয়ে দিলাম। বিষয়টা তেমন না। বরং, ওষুধগুলোকে এমনভাবে ডিজাইন করা হয় যেন সেগুলো নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে ঠিক সেই কাজটা করে, যেটা তাদের করতে হবে—যেমন তালা ও চাবির মতো।
এখানে বিজ্ঞানীরা ওষুধকে এমনভাবে তৈরি করেন যেন এটি আমাদের শরীরে সঠিক সেক্টরে গিয়ে ঠিকভাবে কাজ করে। একে তালা-চাবির মতো বলা যেতে পারে, যেখানে তালা হলো আমাদের দেহের রিসেপ্টর বা নির্দিষ্ট প্রোটিন, আর চাবি হলো ওষুধ। ওষুধটি দেহের অন্যান্য স্থানে না গিয়ে ঠিক সেই রিসেপ্টর বা প্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং সেখানে গিয়ে নির্দিষ্ট কাজটি সম্পন্ন করে।
এই কিছুদিন আগে বিজ্ঞানীরা কোভিড সমস্যার সমাধানের জন্য নানা ধরনের গবেষণা ও চিন্তাভাবনা করেছেন। তারা নতুন ওষুধ আবিষ্কারের জন্য ভাইরাসের গঠন বা স্ট্রাকচার নিয়ে কাজ করেছেন। তারা এমন উপাদান খুঁজেছেন, যা ভাইরাসের স্ট্রাকচারে গিয়ে বসবে এবং সেটিকে নিষ্ক্রিয় বা নষ্ট করে দেবে।
আমরা যদি অ্যান্টিবায়োটিকের উদাহরণ দেখি, যেমন ধরুন, অ্যামোক্সিসিলিন। অ্যামোক্সিসিলিন কীভাবে কাজ করে? যখন আমরা অ্যামোক্সিসিলিন খাই, এটি আমাদের শরীরে থাকা নির্দিষ্ট ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলে। তবে এটি সব ধরনের ব্যাকটেরিয়াকে মারতে পারে না, বরং অ্যামোক্সিসিলিনের জন্য যে ব্যাকটেরিয়াগুলো স্পেসিফিক বা সংবেদনশীল, শুধুমাত্র সেই ব্যাকটেরিয়াগুলোকে মেরে ফেলে।
তার মানে, ওষুধগুলোকে এমনভাবে তৈরি করা হচ্ছে যেন তারা নির্দিষ্ট কিছু স্থানে গিয়ে সুনির্দিষ্ট কাজ করতে পারে। প্রতিটি ওষুধকে এমনভাবে স্ট্রাকচার করা হয় যে, এটি শরীরের সেই নির্দিষ্ট রিসেপ্টরে গিয়ে কাজ করবে, যা তার জন্য নির্ধারিত।
যদি আমরা সহজভাবে ব্যাপারটা বুঝি, তাহলে বলা যায়, ওষুধগুলো আমাদের দেহের রিসেপ্টরে গিয়ে কাজ করে। প্রতিটি রিসেপ্টর নির্দিষ্ট ওষুধের জন্য তৈরি, এবং সেই ওষুধ রিসেপ্টরে গিয়ে তার কার্যক্রম শুরু করে।
তবে সব ওষুধই রিসেপ্টরের ওপর নির্ভরশীল নয়। যেমন অ্যান্টাসিডের ক্ষেত্রে, এটি কোনও রিসেপ্টরে বসে কাজ করে না, বরং এটি সরাসরি একটি রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে পাকস্থলীর অতিরিক্ত অ্যাসিডকে নিরপেক্ষ করে।
রিসেপ্টর ছাড়াও কিছু ওষুধ আরও ভিন্নভাবে কাজ করে। যেমন, ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধগুলি আমাদের দেহের কোনও রিসেপ্টরের ওপর নির্ভর করে না। এর পরিবর্তে, এগুলো সরাসরি শরীরে সংক্রমণ করা ব্যাকটেরিয়ার উপর আক্রমণ করে। এটি সংক্রমিত অংশে গিয়ে স্পেসিফিক ব্যাকটেরিয়াগুলোকে ধ্বংস করে।
আশা করি আপনি এখন বুঝতে পেরেছেন যে, ওষুধ কীভাবে বোঝে কোথায় কাজ করতে হবে বা কিভাবে কাজ করে এবং বিভিন্ন ধরনের ওষুধের কাজের ধরন কীভাবে আলাদা হতে পারে। প্রতিটি ওষুধের কাজ নির্ভর করে তার গঠন এবং সে শরীরের কোন অংশে বা কোন প্রক্রিয়ায় কাজ করছে তার ওপর।